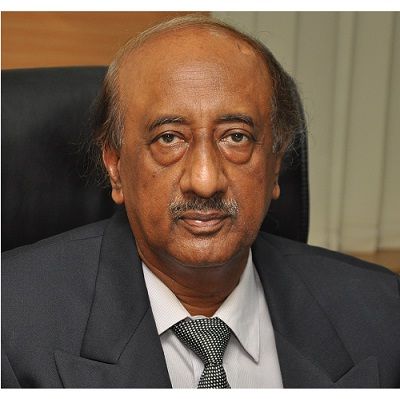বাংলাদেশে অর্থনীতির বেশি পরিচিত সূচকগুলো আপাতদৃষ্টিতে ঠিকই আছে। এখন পর্যন্ত প্রত্যাশিত দিকে প্রত্যাশিত লয়ে এগোচ্ছে। পরিচিত সূচকগুলোর মধ্যে রয়েছে জিডিপি, প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয়, রপ্তানি, রেমিট্যান্স, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, খাদ্যশস্য উৎপাদন, দারিদ্র্যের হার, গড় আয়ু ইত্যাদি। বাজেট ঘাটতি/উদ্বৃত্ত, খেলাপি ঋণের পরিমাণ, শেয়ারবাজারের সূচক, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, কু-ঋণ, আয় ও সম্পদের বৈষম্য, অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি, মুদ্রা সরবরাহ ও মূল্যস্ফীতির পরিমাণ, আদায়কৃত কর-জিডিপির অনুপাত, ব্যালান্স অব ট্রেড/পেমেন্ট-সংক্রান্ত সূচকগুলো খুব পরিচিত না হলেও দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য বোঝার জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অতি পরিচিত সূচকগুলো থেকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ভাসাভাসা ধারণা পাওয়া গেলেও অর্থনীতির অন্তর্নিহিত অবস্থা এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কা-সম্ভাবনা সম্পর্কে অর্থবহ ধারণা পাওয়া যায় না। এ ধারণার জন্য কম পরিচিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলোকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। এ সূচকগুলোর গতি-প্রকৃতির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ থেকে আভাস পাওয়া যাবে মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনীতির অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে।
বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশ এখনো ক্ষুদ্র শক্তি হিসেবে বিবেচিত। অর্থনীতির পরিভাষায় একে ‘Small Country Case’ বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে, বিশ্ববাণিজ্য বা বিশ্ব অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমাদের দর-কষাকষির শক্তি একেবারেই সীমিত। বড় বড় দেশের মধ্যে দর-কষাকষির (Bargaining) ভিত্তিতে যে যে দাম, চাহিদা ও সরবরাহ নির্ধারিত হয়, আমরা তাকে অপরিবর্তনীয় ধরে নিয়ে কর্মকাণ্ড সাজাই। সুবিধা হলো, প্রান্তে অবস্থান করার ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে বয়ে যাওয়া বড় ঝড়-ঝাপটা অনেক সময় সরাসরি আমাদের গায়ে লাগে না। তবে পরোক্ষভাবে বিলম্বে হলেও এর অভিঘাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি। মন্দার প্রভাবে যদি উন্নত দেশগুলোতে চাহিদা হ্রাস পায়, উৎপাদন কমে যায়, আমদানি সীমিত হয়ে পড়ে এবং একই সঙ্গে শ্রমিক ছাঁটাই হয়, তবে তার নেতিবাচক প্রভাব যে আমাদের দেশের ওপর পড়বে, তাতে সন্দেহ নেই।
বিশ্বের উন্নত (ধনী) দেশগুলোতে মন্দার কালো ছায়া পড়তে শুরু করেছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, চীন-যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধ। এক দেশ অন্য দেশের ওপর তালাতালি করে শুল্ক আরোপ করছে, যার ফলে বিশ্ববাণিজ্য ব্যাহত হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত নিজের দেশে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কমে যাচ্ছে। শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত দেশগুলোতে চাহিদা হ্রাসের সঙ্গে আমদানি কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশ দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তার রপ্তানিপণ্য, বিশেষ করে তৈরি পোশাক বিদেশের বাজারে বিক্রি করা ক্রমেই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। বিদেশে উৎপাদন কমে গেলে শ্রমিক ছাঁটাই হবে এবং ফলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়ে যাবে। বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের একাংশ দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হবে।
মন্দার প্রভাব পড়েছে চীন, ভারত, জাপান, সিঙ্গাপুরসহ এশিয়ার আরো কয়েকটি দেশে। চীনে জিডিপির প্রবৃদ্ধি কমে দাঁড়িয়েছে ৬.২ শতাংশে, যা ১৯৯০ সালের পর সর্বনিম্ন। চীনের রপ্তানির ২০ শতাংশ যায় যুক্তরাষ্ট্রে। রপ্তানি ব্যাহত হওয়ায় চীনের ব্যবসায়ীরা উদ্বিগ্ন। অনিশ্চয়তার মধ্যে তাঁরা উৎপাদন পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে তৈরি করতে পারছেন না। ভারতের অবস্থাও তথৈবচ। ভারতে জিডিপির প্রবৃদ্ধি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়েই চলছিল। প্রবৃদ্ধির সেই গতি থমকে গেছে। প্রবৃদ্ধির হার কমে গিয়ে ৫.৬ শতাংশে চলে এসেছে। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার একাধিকবার কমিয়েও প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখতে পারেনি। বাণিজ্যযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ হার বাড়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকংয়ের অবস্থাও পড়তির দিকে। জাপানের মতো সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানির বড় অংশ হচ্ছে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম। এগুলোর চাহিদা কমে যাওয়ায় তাদের অর্থনীতি সংকটে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ব্যাবসায়িক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নিকটবর্তী দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমস্যার আঁচ যে বাংলাদেশের গায়ে লাগবে না—এমন কথা নিশ্চিন্তভাবে বলা যায় না। অর্থনীতির সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার লক্ষ্যে বিষয়টির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন রয়েছে।
মন্দার আঁচড় সাধারণত প্রথম দিকে লাগে পুঁজিবাজারের (Capital Market) মতো স্পর্শকাতর অঙ্গনে। পুঁজিবাজারের বড় বিনিয়োগকারীরা প্রতিদিন নিয়মিত তাদের বিনিয়োগের ওপর লাভ-ক্ষতির সম্ভাবনা/আশঙ্কা খতিয়ে দেখেন। সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতির আলোকে তাঁরা বিনিয়োগ বাড়ানো-কমানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্য এর সঙ্গে নানারূপ অনৈতিক ব্যাবসায়িক চাল জড়িত থাকে। যদি তাঁদের দৃষ্টিতে নিকট ভবিষ্যতে অর্থনীতির অঙ্গনে গুমট হাওয়া তাল পাকাতে থাকে অথবা কালো মেঘের আনাগোনা পরিলক্ষিত হয়, তবে তাঁরা নতুন বিনিয়োগে অনাগ্রহী হন, পুরনো বিনিয়োগ সরিয়ে নিতে প্রয়াসী হন। পুঁজিবাজারের সূচকের পতন ঘটে। কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে সামগ্রিক ধারায় সূচকের পতন ঘটেছে। কয়েক দিন পর হঠাৎ এক বা দুই দিন সূচকের উত্থান ঘটলেও তা টেকসই হয় না, দুই দিনের মধ্যে আবার পতন শুরু হয়। এভাবে কমতে কমতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক ৫০০০-এর কাছাকাছি এসে পড়েছে। আগের সময়ের তুলনায় তা দৃষ্টিকটুভাবে কম। নিকট ভবিষ্যতে বড় রকমের উত্থান আশা করা যায় না। অর্থনীতির জন্য এটি নিঃসন্দেহে অশনিসংকেত।
দেশের মধ্যে যে সেক্টর দারুণ উদ্বেগ-আশঙ্কায় পূর্ণ, তা হলো ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাত, যাকে আমরা নন-ব্যাংকিং ফিন্যানশিয়াল ইনস্টিটিউশন (NBFI) বলে জানি। দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় আর্থিক অঙ্গনের এ অংশটি জর্জরিত। পুরো অর্থনীতির ওপর তা এক মহা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের এক বিরাট অংশ খেলাপি এবং কু-ঋণ হয়ে গেছে। এ অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ফলে ব্যাংকগুলো প্রভিশন ঘাটতি, মূলধন ঘাটতিসহ নানাবিধ সমস্যায় ভুগছে। বাজেট থেকে ভর্তুকি বা অনুদানের সুবিধা না পেলে অনেক ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। জনগণের টাকায় রুগ্ণ ব্যাংকগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে এগুলো ধসে না পড়ে। কারণ ব্যাংক ধসে পড়লে জনসাধারণের আস্থার জগতে যে চিড় ধরবে, তা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে বিপদগ্রস্ত করে তুলবে। এত বড় সরকারি সমর্থনের পরও আমানতকারীদের আস্থা সম্পূর্ণরূপে পুনঃস্থাপিত করা যাচ্ছে না। ব্যাংকে টাকা রাখতে আমানতকারীরা ভয় পাচ্ছে। ফলে ব্যাংকে তারল্য সংকট সৃষ্টি হয়েছে। নন-ব্যাংকিং ফিন্যানশিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো বেশি মুনাফা দিয়ে আমানত সংগ্রহ করছে। ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের টাকা লক্ষ্যবিচ্যুত হয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এক বিরাট অংশ বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে, এ পর্যন্ত কমবেশি সোয়া পাঁচ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। এটি দেশের জন্য নিখাদ ক্ষতি (Dead Weight Loss)| আরো হতাশার ব্যাপার হচ্ছে, এশিয়াসহ বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ খেলাপি ঋণের হার কমিয়ে এনেছে। বড় অর্থনীতির দেশগুলোর বেশির ভাগের খেলাপি ঋণের হার ৫ শতাংশের নিচে; তার বিপরীত অবস্থা বাংলাদেশে। এ বছরের মার্চ মাসে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২ শতাংশে। খেলাপি ঋণের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। ২০১১ সালে এর পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৬৪৪ কোটি টাকা। ২০১৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে এক লাখ ১০ হাজার ৮৭৩ কোটি টাকা (১,১০,৮৭৩)।
সরকারের রাজস্বপ্রাপ্তি এবং বাজেট ঘাটতির পরিমাণ সুখকর নয়। ভবিষ্যতে এ অবস্থার অবনতি ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। এ বছরে সংশোধিত বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব সংগ্রহে ঘাটতি হয়েছে ৫৬ হাজার কোটি টাকা। মূল বাজেটের হিসাবে এর পরিমাণ আরো বেশি। সরকারি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, ২০১৫ সাল থেকে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছে। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ঘাটতির পরিমাণ লাফিয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এদিকে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সুদ পরিশোধের পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাচ্ছে। এমন ধারা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে আবর্তক এবং উন্নয়ন বাজেটের জন্য অর্থসংস্থান সহজসাধ্য হবে না। তখন জনগণের ওপর কর, সম্পূরক কর, ফি, চার্জ এবং রাষ্ট্রীয় খাতে উৎপাদিত পণ্যের বর্ধিত দাম অসহনীয় হয়ে পড়তে পারে, যার প্রতিক্রিয়া সরকারের জন্য ভালো হবে না। পুরো ব্যাপারটা সরকারের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেবে।
সরকারের বাজেট বাস্তবায়ন, বিশেষ করে উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার একটি দুর্বল এলাকা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাজেটের আকার দৃশ্যমানভাবে বেড়েছে। ২০০৯-১০ সালে সামগ্রিক বাজেটের আকার ছিল এক লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ সালে তার আকার দাঁড়িয়েছে চার লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা। ২০১৯ সালে বাজেটের আকার পাঁচ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। বাজেট বাস্তবায়নের হার মোটামুটি ৮০ শতাংশের কাছাকাছি। মার্চের দিকে উন্নয়ন বাজেট সংশোধন করে মূল বাজেটের থেকে তার পরিমাণ অনেক কমিয়ে আনা হয়। তার পরও এপ্রিল-মে মাসে দেখা যায়, ১০-১১ মাসে উন্নয়ন বাজেটের মাত্র ৬০-৬৫ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ মাসে গড় বাস্তবায়ন ৫ শতাংশ। জুন মাসে প্রকৃত বাস্তবায়নের বস্তুনিষ্ঠ হিসাব-নিকাশ ছাড়া আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে ঘোষণা করা হয় যে উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৯০ শতাংশ বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। জুলাই মাসে ঘুরেফিরে এ সংখ্যাটাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়। তবে সম্পন্নকৃত প্রকল্পের সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম থাকে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য থেকে বোঝা যায়, মাত্র এক মাসে উন্নয়ন বাজেটের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এটি বাস্তবানুগও নয়। পরবর্তীকালে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আইএমইডির রিপোর্ট থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্প বাস্তবায়নে আমাদের বড় রকমের ঘাটতি রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের আরো বাস্তববাদী এবং তৎপর হতে হবে।
আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ একই ধারায় (Secularly) বেড়ে চলছিল। এ ধারা বজায় থাকলে রিজার্ভের পরিমাণ এত দিনে ৪০ বিলিয়নের কাছাকাছি চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি; এটি ৩২ বিলিয়নের আশপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, কোনো কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের টানা বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বিষয়টি কঠিন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে টাকার বিনিময় হার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সরকারি অবস্থান এবং কার্ব মার্কেটের বাস্তবতা সংগতিপূর্ণ মনে হয় না। বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ থেকে ডলার ছেড়ে বিনিময় হারের পার্থক্য কমাতে চেষ্টা করে। আপাতত তারা সফল রয়েছে। তবে কত দিন এ সফলতা ধরে রাখতে পারবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বিপুল রিজার্ভ থাকা সত্ত্বেও ভারতের কর্তৃপক্ষ তাদের মুদ্রার মান ধরে রাখতে পারেনি। মুদ্রার মান ধরে রাখা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এর থেকে অন্যত্র দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে হয়তো আরো কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে।
অর্থনীতির আরো কয়েকটি চ্যালেঞ্জ আলো-ছায়ায় অবস্থান করছে। কালক্রমে এগুলো দৃশ্যমান হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চামড়াজাত পণ্যের হ্রাসকৃত চাহিদা, বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন রক্ষা ও বাজারজাতকরণ সমস্যা, রড ও ইস্পাতের হঠাৎ চাহিদার পতন ইত্যাদি। এ নিবন্ধের মূল কথা হলো যে আবছা আলোতে সমস্যার নর্তনকুর্দন দেখেও আমরা নিশ্চিন্তে থাকি। তারপর হঠাৎ করে শুনতে পাই, অর্থনীতির কোনো এক অংশে বড় সমস্যার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, যা পুরো অর্থনীতিকে ভারাক্রান্ত করছে। আমরা তখন অসহায় বোধ করি। আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ২০১৭ সালে সিলেট-সুনামগঞ্জে অকালবন্যার প্রাক্কালে সরকারি গুদামে চালের মজুদ মারাত্মকভাবে কমে গিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ তাতে গা লাগায়নি। চাল আমদানিতে তখনো শুল্ক আরোপিত ছিল ২৮ শতাংশ। বন্যার পর জাতি জানতে পারল, আমাদের চালের মজুদ তলানিতে ঠেকেছে। তড়িঘড়ি করে বিশ্ববাজার থেকে চাল কেনার প্রক্রিয়া শুরু হলো। আমদানি শুল্ক কমিয়ে ২ শতাংশে আনা হলো। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা, সেবার সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযান ব্যর্থ হলো। মন্ত্রী ব্যর্থতা স্বীকার করলেন। কিন্তু দায় স্বীকার করে সরে গেলেন না। খাদ্যের মজুদ বাড়ানোর প্রয়োজনে চাল আমদানি অতি সহজ করা হলো। এবার দোলক চলে গেল অন্য প্রান্তে। আমদানীকৃত চালে বাজার সয়লাব হয়ে গেল। ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে চালের দর প্রতি কেজি ৩০-৩২ টাকায় নেমে এলো। কর্তাব্যক্তিরা তা ভালোভাবে দেখতে পেলেন বলে মনে হলো না। তাঁরা টের পেলেন অনেক পরে, কৃষক যখন উৎপাদিত ধানের মূল্য না পেয়ে রাস্তায় ধান ছড়িয়ে প্রতিবাদ করতে শুরু করল তখন। উপায়ান্তর না দেখে আমদানি শুল্ক আবার বাড়ানো হলো। সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র প্রতিকারমূলক যেসব পদক্ষেপ তাত্ক্ষণিকভাবে নেওয়া যেত, তা নিতে বিলম্ব হওয়ায় পরবর্তীকালে বিশাল সমস্যার মোকাবেলা করতে হলো।
চামড়াজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের যে সমস্যা হচ্ছে, তা-ও আমরা যথাসময়ে জানতে পারিনি। জানলাম অনেক পরে, যখন দেশে চামড়ার বাজারে ধস নেমেছে। ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে দুই সিটি করপোরেশন রোগের প্রাদুর্ভাবের আভাস পেয়েছিল অনেক আগে। তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ডজন-ডজন রোগী মারা যাওয়ার পর তাদের বোধোদয় হয়েছে। অথচ ঠিক সময়ে অর্থাৎ বিপত্সংকেত পাওয়া মাত্র পদক্ষেপ নিলে হয়তো এত লোক আক্রান্ত হতো না।
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। হালকা সমস্যা গণ্য করে এসব বিপত্সংকেতকে উড়িয়ে না দিয়ে ভবিষ্যতের ভুক্তভোগী এবং অংশীজনকে (Stakeholder) সঙ্গে নিয়ে তাত্ক্ষণিকভাবে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি নিলে বড় বিপর্যয় এড়াতে পারি। সাবধানের মার নেই। সময় থাকতে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। এ কথা-সে কথা বলে পাশ কাটিয়ে গেলে সমস্যা দানবের আকার ধারণ করবে।
লেখক : সাবেক মন্ত্রিপরিষদসচিব ও পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান