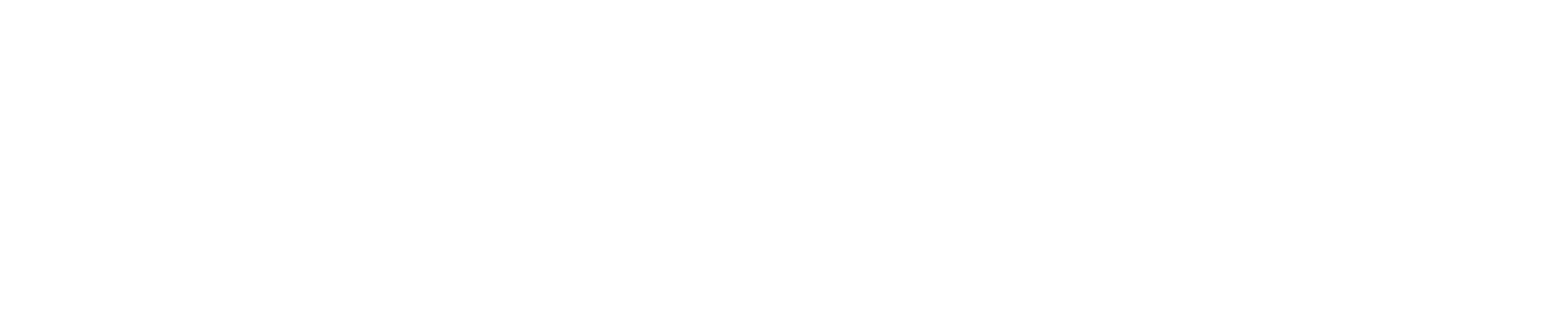নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার একজন জনপ্রিয় নেতা। শুধু বর্ণবাদী শাসনের অবসান ঘটানো একজন নেতা নন; তিনি বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী এক মহানায়ক। তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা অতীতের দুঃসহ বিভাজন থেকে মুক্তি পেয়েছে, তবে প্রতিশোধের পথে না গিয়ে সত্য ও পুনর্মিলনের মাধ্যমে একটি নতুন জাতি গঠনের প্রয়াস পেয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, শুধু প্রতিহিংসা নয়, বরং ইতিহাসের নির্মম সত্যকে স্বীকার করে, অপরাধীদের দায় স্বীকার করিয়ে এবং ভুক্তভোগীদের কণ্ঠকে গুরুত্ব দিয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। এ কারণেই তিনি ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন’ গঠন করেছিলেন, যা অতীতের অপরাধ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি জনগণের মধ্যে পুনর্মিলন ও পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ তৈরি করেছিল।
বাংলাদেশেও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়, কিন্তু এর পরপরই জাতি গভীর বিভাজনের শিকার হয়। একদিকে ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তির প্রশ্ন, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার সংস্কৃতি। স্বাধীনতার পর নানা রকম আশার আলো জ্বলে উঠলেও তা রাজনৈতিক নেতৃত্বের অদূরদর্শিতার কারণে স্থায়ী কোনো রূপ নিতে পারেনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের হত্যাকাণ্ড, এরপর সামরিক শাসনের দীর্ঘ সময়, গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তী সময়ে প্রতিটি নির্বাচনের পর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর দমন-পীড়ন চলতে থাকে। ফলে বাংলাদেশে ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন’ ধরনের কোনো প্রক্রিয়া সম্ভব হয়নি।
দক্ষিণ আফ্রিকার বাস্তবতা ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বর্ণবাদী শাসন, যেখানে শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুরা কালো সংখ্যাগরিষ্ঠদের ওপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিপীড়ন চালিয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার অপরাধীরা ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর স্থানীয় দোসর, যারা নিজ জাতির মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। স্বাধীনতার পর এই অপরাধীদের বিচার না হওয়া এবং রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত হওয়া জাতির বিভাজনকে বাড়িয়ে দেয়।
বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবির বিষয়ে ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন করা হলেও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বরং ১৯৭৫ সালের পর যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসন এবং রাজনীতিতে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয়। ফলে ন্যায়বিচারের বদলে প্রতিহিংসার রাজনীতি আরও দৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়ে। ২০০৯ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হলেও সেটি রাজনৈতিক বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি।
বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিভাজন এবং প্রতিহিংসার সংস্কৃতি এতটাই প্রবল যে ম্যান্ডেলার মডেল এখানে বাস্তবায়ন করা কঠিন। কারণ, ন্যায়বিচার ও পুনর্মিলন একসঙ্গে করতে হলে নিরপেক্ষতা ও আস্থার পরিবেশ থাকা প্রয়োজন, যা বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দীর্ঘদিনের অবিশ্বাস, প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন থাকায় কোনো সত্য কমিশন গঠন করলেও তা বিশ্বাসযোগ্য হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সহিংসতা ও দমন-পীড়নের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৯৯০-এর পর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরে এলেও প্রতিটি নির্বাচন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় সহিংসতা এবং বিরোধী দল দমনের ঘটনা ঘটেছে। ২০০৪ সালের গ্রেনেড হামলা, ২০১৩-১৪ সালের রাজনৈতিক সহিংসতা, ২০০৯ সালের বিডিআর বিদ্রোহ—এসব ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হয়নি। ফলে শুধু ১৯৭১ সালের নয়, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সহিংসতার ক্ষেত্রেও ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন’ কমিশনের মতো কিছু করা দরকার।
বাংলাদেশ যদি সত্যিকার অর্থে ম্যান্ডেলার পথ অনুসরণ করতে চায়, তাহলে প্রথমত রাজনৈতিক প্রতিহিংসার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিচারব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে, যাতে কোনো অপরাধীর শাস্তি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক না থাকে। তৃতীয়ত, অতীতের অন্যায়ের স্বীকারোক্তি এবং ভুক্তভোগীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অপরাধীরা প্রকাশ্যে এসে তাদের অপরাধ স্বীকার করেছিল, কিন্তু বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে অপরাধ স্বীকারের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি।
দুই.
বাংলাদেশে ন্যায়বিচার ও পুনর্মিলনের প্রশ্নটি কেবল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পালাবদলের প্রতিটি পর্বই রক্তাক্ত এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বিষে ভরা। শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক শাসকদের অধীনে দেশে একধরনের বিচারহীনতার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এ পরিস্থিতির ধারাবাহিকতায় ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন। ১৯৮২ সালে এরশাদ ক্ষমতা দখলের পর তাঁর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেটা দমনে সহিংসতা কম হয়নি। ১৯৯১ সালে ও ১৯৯৬ সালে ক্ষমতার পালাবদলের সময়ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ওপর সহিংসতা হয়েছে। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগের কর্মীদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন চলে। দেশের সবগুলো জেলায় একযোগে বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। তা ছাড়া, আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা চালানোয় ২৪ জনের প্রাণহানি ও অসংখ্য মানুষ আহত হয়।
এরপর ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হতে না হতেই বিডিআর বিদ্রোহের নামে এক লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞ ঘটে। ২০১৩-১৪ সালে রাজনৈতিক সহিংসতায় অনেক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনামলে গুম-খুন, মামলা-হামলার অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। বিরোধী দল দমনে সরকারি বাহিনীগুলোর আচরণ ছিল নিষ্ঠুর। এসব ঘটনার কোনোটিরই নিরপেক্ষ তদন্ত হয়নি, হয়নি পুনর্মিলনের উদ্যোগ। ফলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিভাজন ক্রমাগত বেড়েছে।
এ প্রেক্ষাপটে সত্য ও পুনর্মিলনের প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত, ন্যায়বিচার ও পুনর্মিলন একসঙ্গে চলতে হলে সত্য প্রকাশ করতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন’-এর মতো একটি নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনাগুলো অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এটি এমন একটি কাঠামো হতে হবে, যেখানে রাজনৈতিক দল ও সাধারণ জনগণের আস্থা থাকবে এবং যা শুধু প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না।
দ্বিতীয়ত, প্রতিটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও সহিংসতার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দায় নির্ধারণের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় দেখা যায়, যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, তারা অপরাধীদের রক্ষা করে এবং বিরোধীদের দমন করে। এই প্রবণতা বন্ধ না হলে পুনর্মিলন সম্ভব নয়।
তৃতীয়ত, শুধু বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, জাতির ঐক্যের স্বার্থে একটি স্বীকারোক্তির পরিবেশ তৈরি করতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অপরাধীরা প্রকাশ্যে তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা কখনোই অপরাধ স্বীকার করেন না; বরং প্রতিটি সরকার ক্ষমতায় এসে নতুন করে ইতিহাস লেখার চেষ্টা করে।
চতুর্থত, শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে অতীতের সত্য তুলে ধরা দরকার। বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠক্রম বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে, যার ফলে একেক সময় একেক ধরনের সত্য প্রচার করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ, সামরিক শাসন, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড—এসব বিষয়ে একটি একক, গ্রহণযোগ্য ঐতিহাসিক বয়ান থাকতে হবে, যাতে নতুন প্রজন্ম সঠিক ইতিহাস জানতে পারে এবং সত্যের ভিত্তিতে একে অপরকে বোঝার সুযোগ পায়।
বাংলাদেশে ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন’ কমিশনের মতো কোনো উদ্যোগ সফল করতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমত, এটি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান হওয়া যাবে না; বরং বিচার বিভাগের অধীনে স্বাধীন কমিশন হিসেবে কাজ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কমিশনে সব রাজনৈতিক পক্ষের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে, যাতে কোনো পক্ষ এটিকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহারের অভিযোগ তুলতে না পারে। তৃতীয়ত, শুধু অতীতের বিচার নয়, ভবিষ্যতে প্রতিহিংসার রাজনীতি বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে। যদি প্রতিহিংসার চক্র চলতেই থাকে, তাহলে কোনো পুনর্মিলন সম্ভব হবে না।
নেলসন ম্যান্ডেলার সফলতার পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব। তিনি শুধু ক্ষমা করার কথা বলেননি, বরং সত্যকে গ্রহণ করে, দোষীদের জবাবদিহির আওতায় এনে এবং সর্বোপরি বিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে একটি কার্যকর ব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন। বাংলাদেশে তেমন একজন তেজোদীপ্ত নেতা থাকলেও তাঁকে দলীয় বৃত্তে বন্দী করে বিতর্কিত করা হয়েছে। এখানে ক্ষমতার জন্য লড়াই চলে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ঐক্যের জন্য কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে দেখা যায় না।
তবে বাংলাদেশে সত্য ও পুনর্মিলনের মডেল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে, এমন বলা যায় না। যদি রাজনৈতিক নেতৃত্ব সত্যিকার অর্থে এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, যদি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিরপেক্ষ রাখা যায়, যদি জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়—তাহলে একটি নতুন ঐক্য প্রক্রিয়া গড়ে তোলা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে শুধু ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন’ নয়, বরং একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ প্রয়োজন, যেখানে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার নীতি পরিহার করে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা হবে।
বাংলাদেশের জন্য ম্যান্ডেলার পথ কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। একমাত্র শর্ত হলো সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস এবং অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার সদিচ্ছা। যদি সেটা সম্ভব হয়, তবে বাংলাদেশেও একদিন ন্যায়বিচার ও পুনর্মিলনের একটি গ্রহণযোগ্য পথ রচনা করা যাবে।
লেখক : জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, কলামিস্ট