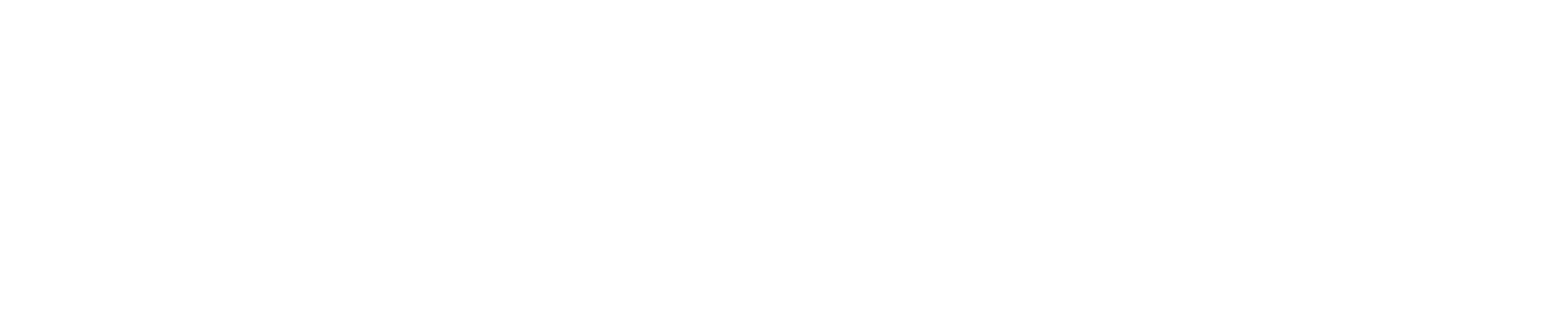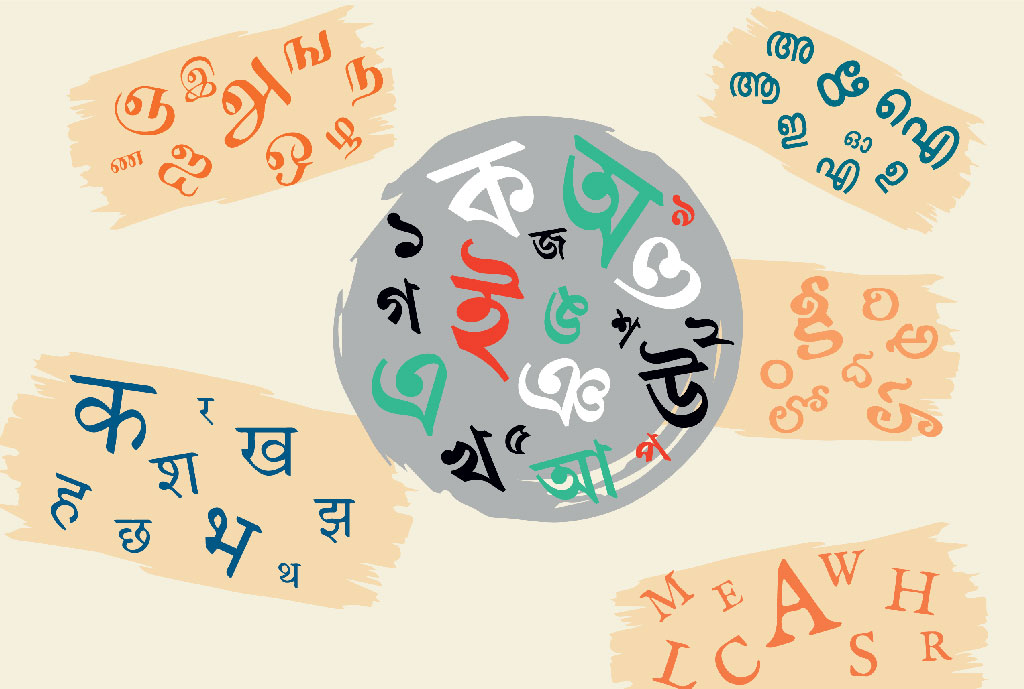ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮) যে ধরা পড়েছিলেন সে তাঁর ভাষার কারণে। তরুণ ক্ষুদিরাম তরুণ প্রফুল্ল চাকীকে (১৮৮৮-১৯০৮) সঙ্গে নিয়ে বিহারের মুজাফফরপুরে গিয়েছিলেন এক দুর্বৃত্ত ইংরেজকে হত্যা করতে। রাতের অন্ধকারে ওই ম্যাজিস্ট্রেটের ঘোড়ার গাড়ি লক্ষ্য করে তাঁরা বোমা ছোড়েন, তারপর দুজনে দুদিকে মিলিয়ে যান, অন্ধকারে। সারা রাত ধরে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে অভুক্ত ক্ষুদিরাম এক মুদিদোকানে গিয়ে মুড়ি চেয়েছিলেন। তাঁর উচ্চারণই ধরিয়ে দিল তাঁকে। অবাঙালি দোকানদারের ধারণা হলো যুবকটি স্থানীয় নয়, ইতিমধ্যে রটে গিয়েছিল বোমা নিক্ষেপের খবর, দোকানদারের সন্দেহ হলো যুবক হয়তো ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। তাতেই গ্রেপ্তার হলেন ক্ষুদিরাম, এর পরে তাঁর ফাঁসি। প্রফুল্ল চাকী প্রথমে তাঁর ভাষার জন্য ধরা পড়েননি, বরং আশ্রয় পেয়েছিলেন। কিন্তু পরে ধরা পড়লেন এই ভাষার কারণেই।
সারা রাত একটানা দৌড়ে প্রফুল্ল চাকী সকালে পৌঁছেছিলেন এক রেলস্টেশনের কাছে। রেলের একজন বাঙালি কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলতেই লোকটি চিনে ফেলল যে যুবকটি বাঙালি এবং সেও সন্দেহ করল যে যুবক বোমা হামলার সঙ্গে যুক্ত। ক্লান্ত অভুক্ত প্রফুল্ল চাকীকে বাঙালি রেল কর্মচারী নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। খেতে দিল, নতুন জামাকাপড় কিনে দিল বাজার থেকে, জুতাও এনে দিল এক জোড়া, তারপর রাতের বেলা তুলে দিল এক ট্রেনে। লোকটি নিশ্চয় জাতীয়তাবাদী ছিল, মনে মনে। প্রফুল্ল চাকী ট্রেনে উঠলেন। ট্রেনের ওই কামরায় ছিল আরেক বাঙালি। লোকটি ছিল পুলিশের চর। প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে আলাপ করে তার সন্দেহ হয়। সন্দেহ হওয়ায় সেও জাতীয়তাবাদী সাজল এবং এক ফাঁকে নেমে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ধরিয়ে দিল প্রফুল্ল চাকীকে। প্রফুল্ল চাকীর ফাঁসি হয়নি, কেননা ঘটনাস্থলেই তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন, বিষ খেয়ে। বিষের কৌটা তাঁর সঙ্গেই ছিল।
ভাষা এই কাজটা করে, পরিচয় জানিয়ে দেয়। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ওই পরিচয়। মানুষের পক্ষে ধর্মান্তরিত হওয়া কঠিন নয়, ভাষান্তরিত হওয়া কঠিনতর।
প্রফুল্ল চাকী হয়তো গ্রেপ্তার হতেনই, শেষ পর্যন্ত; কিন্তু অত সহজে হয়তো হতেন না, যদি না তাঁদের ভাষাগত পরিচয়টা অমন স্পষ্ট হতো। ভাষা প্রফুল্ল চাকীকে যুক্ত করে দিয়েছিল রেলের ওই বাঙালি কর্মচারীটির সঙ্গে, যে নাকি বিপদ হতে পারে জেনেও আশ্রয় ও সমর্থন দিয়েছে প্রফুল্ল চাকীকে। ভাষা ওই কাজটাও করে। কাছে আনে। পারে ঐক্যবদ্ধ করতে। করেও। কিন্তু আবার বিচ্ছিন্নও তো করে, প্রফুল্ল চাকীকে যেমন করেছিল, দ্বিতীয় বাঙালিটির ক্ষেত্রে, যে তাঁকে ধরিয়ে দিল, চাকরিতে উন্নতি হবে এই লোভে। এই ক্ষেত্রে দোষটা অবশ্য ভাষার নয়, দোষটা স্বার্থের। পুলিশের টিকটিকিটি ভাষাগত আত্মীয়তা খোঁজেনি, নিজের স্বার্থ দেখেছে। স্বার্থ কি প্রথম বাঙালিটি দেখেনি, রেলের সেই বাঙালি কর্মচারীটি? দেখেছে।
জাতীয়তাবাদ নিঃস্বার্থ নয়, সেও স্বার্থদ্রষ্টা। কিন্তু জাতীয়তাবাদী স্বার্থটা সমষ্টিগত, সেটা চাকরির প্রমোশনের স্বপ্ন নয়, জাতিকে মুক্ত করবার আকাঙ্ক্ষা। সমষ্টিগত স্বার্থের ওই বোধ যখন প্রবল হয়, তখন মানুষ প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকে, যেমন দিয়েছেন ক্ষুদিরাম, দিয়েছেন প্রফুল্ল চাকী। বিপদের ঝুঁকি নেয়, যেমন নিয়েছে রেলের ওই নাম না-জানা কর্মচারীটি। আর কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ যে দেখে, সে কী ধরনের আচরণ করতে পারে তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছে পুলিশের ওই ভৃত্যটি। সব কজনই বাঙালি; কিন্তু কত তফাত।
জাতীয়তাবাদ একটা অনুভূতির ব্যাপার। সেই অনুভূতির ভেতরে একটা স্বার্থচেতনা থাকে, সেটাই ভিত্তি; কিন্তু অনুভূতিটা স্বার্থচেতনাকে ছাপিয়েও ওঠে। জাতীয়তাবাদীরা সবাই স্বাপ্নিক, এমনকি উগ্র জাতীয়তাবাদী উন্মাদনায় খুবই যারা নিষ্ঠুর, আগ্রাসী, তারাও। ওই স্বপ্নটা একটা কল্পিত দেশের।
জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে অনেক কিছু বলার থাকে এবং তা বলা হয়েছেও। জাতীয়তাবাদের উগ্ররূপ সম্পর্কে বিশ্ব-ইতিহাস করুণভাবে অবহিত। এর কারণে দ্বন্দ্ব বেধেছে, প্রাণ দিয়েছে লাখ লাখ মানুষ, এখনো দিচ্ছে। জাতীয়তাবাদ যখন ফ্যাসিবাদের রূপ নেয়, তখন তারচেয়ে ভয়ংকর বস্তু সত্যি সত্যি বিরল। ১৯১৭ সালে, ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের বেশ আগে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) জাতীয়তাবাদের অশুভ দিকটির কথা বলেছেন। বলেছেন, ‘জাতীয়তাবাদ হচ্ছে বড় হুমকি’। লক্ষ করেছেন যে জাতীয়তাবাদের চালিকাশক্তি হচ্ছে লুণ্ঠনের অতিউগ্র বাসনা।
কিন্তু জাতীয়তাবাদ আরও একটি রূপ নিতে পারে। এই রূপটিকে বলতে পারি গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ। যার লক্ষ্য বঞ্চিত মানুষকে আধিপত্যবাদের হাত থেকে মুক্ত করা, মুক্ত করে জাতির অন্তর্গত সব মানুষের মধ্যে অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এবং সেই সঙ্গে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো। মার্ক্সবাদীরা আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী, কেননা সর্বহারার তো পায়ের নিচে ভূমিই নেই দাঁড়াবার, দেশ পাবে কোথায়? কিন্তু আশ্রয়হীনতা কোনো আদর্শ ব্যাপার নয়, সেটা দুঃখের ব্যাপার। সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের ও সংস্কৃতির বিকাশের প্রয়োজনে একটি ভূমি থাকা দরকার, মানসিক ভূমিও, যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ আগ্রাসন, আধিপত্য, শোষণ, বঞ্চনা ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়বে। লেনিন যে বলেছেন, ‘প্রত্যেক আধুনিক জাতির দুটি করে জাতি আছে। প্রত্যেক জাতীয় সংস্কৃতির দুটি সংস্কৃতি আছে।’ সে বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ওই যে বঞ্চিত অংশ—জাতির ও সংস্কৃতির—তার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমগ্র জনগোষ্ঠীকে একটি জাতিতে পরিণত করা সেও একটা সংগ্রামের ব্যাপার, যে-সংগ্রামটিকে প্রাথমিক পরিচয়ে জাতীয়তাবাদী বললে ভুল বলা হবে না। কমিউনিস্ট ইশতেহারে মার্ক্স-অ্যাঙ্গেলসের বক্তব্যে বাস্তবতার এই দিকটির উল্লেখ আছে: ‘বস্তুগত দিক থেকে না হলেও আকারগত দিক থেকে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সর্বহারাদের সংগ্রাম প্রথমত একটি জাতীয় সংগ্রাম। প্রতিটি দেশের সর্বহারাবাদীকে অবশ্যই সবার আগে তাঁর নিজস্ব বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিষয়গুলো মীমাংসা করতে হবে।’
মার্ক্স-অ্যাঙ্গেলস আরও লিখেছেন, ওই ইশতেহারে, ‘সর্বহারাবাদীদের অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হতে হবে। অবশ্যই জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারার মতো শ্রেণির হতে হবে। জাতি গঠন করতে হবে। যদিও বুর্জোয়ার সঙ্গে সেভাবে মেলে না।’ আগের কাজ আগে। আগে জাতীয় পাওনা-গণ্ডার মীমাংসা করতে হবে, তারপরে আন্তর্জাতিকতাবাদ। আসলে এ ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়, অনুপ্রবিষ্ট বটে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি নয়। সমগ্র জনগণের জাতীয়তাবাদ আর ধনিক শ্রেণির জাতীয়তাবাদ এক বস্তু নয়, চরিত্রগতভাবেই তারা স্বতন্ত্র। কিন্তু দুটোতেই স্বার্থ আছে, একটি স্বার্থ সকলের, অপরটি অল্প কিছু লোকের। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যেকোনো আলোচনায় এই পার্থক্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং থাকার কারণেই জাতীয়তাবাদের ভেতরে যে প্রগতিশীল উপাদান রয়েছে, তা অস্বীকার করা যাবে না। এই জাতীয়তাবাদ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বিকশিত হয়, আর সে নিজেও একটি সংগ্রাম বটে, একটি স্থায়ী সংগ্রাম-মুক্তির লক্ষ্যে।
বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক, যে-জন্য এ জাতীয়তাবাদ ভারতীয় নয়, এবং ছিল না সে পাকিস্তানিও। এ সেই জাতীয়তাবাদ, যা বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী ও রেলের ছোট বাঙালি কর্মচারীটিকে একই সমতলে এনে দেয়, এক করে ফেলে; এবং তার বিপরীত দিকে ক্ষুদিরাম বসুকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে মুজাফফরপুরের অবাঙালি দোকানদারটির কাছ থেকে। বোধের ওই ব্যাপারটা একেবারেই প্রাথমিক। শ্রেণিচেতনার মতো অত শক্তিশালী না হলেও, কাছাকাছি বটে।
লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়