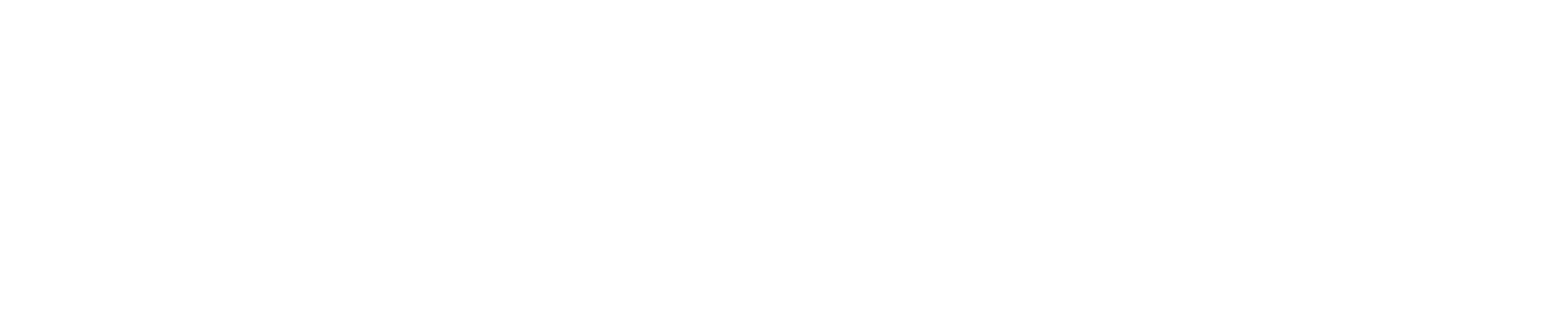বাংলাদেশের রাজনীতি অন্য অনেক দেশের তুলনায় অত্যন্ত মন্দ অবস্থায় পড়েছে। পচে গেছে, ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে, ইতর প্রাণীর কামড়াকামড়ির রূপ নিয়েছে– এসব উপমা ব্যবহার করা অন্যায় নয়, ব্যবহার করা হচ্ছে বৈকি। তা হতে থাকুক, আপত্তি নেই। ধিক্কার যার প্রাপ্য সে ধিকৃত হবে, এটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এর ভেতর থেকে নাগরিকদের মনে যে রাজনীতিবিমুখতা গড়ে উঠবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে, সেটা রীতিমতো বিপজ্জনক। মানুষ সামাজিক প্রাণী– এই সংজ্ঞা প্রাচীন এবং সমাজ যেহেতু রাষ্ট্রের বাইরে নয়, আকাশচারী নয়, ভাসমান নয় নদীতে; মানুষকে তাই রাষ্ট্রের অধীনেও থাকতে হয়। মানুষ রাজনৈতিক প্রাণীও বটে, অনিবার্যভাবেই সত্য সেটা। রাজনীতিবিমুখ হওয়া তাই অমানুষ হওয়াই, আসলে।
বাঙালি অবশ্য খুবই রাজনীতিসচেতন; কিন্তু কোন বাঙালি? না, সব বাঙালি নয়; শ্রমজীবী মানুষ রাজনীতিবিমুখ না হোক, রাজনীতি-উদাসীন বটে। রাজনীতি নিয়ে কথা বলে মধ্যবিত্ত। কথাই বলে মূলত এবং সে আলোচনা আদর্শিক-দার্শনিক স্তরে ওঠে না প্রায় কখনোই; ব্যক্তি, বড়জোর দল নিয়েই নাড়াচাড়া করে। গুজব রটায়, কুৎসা ছড়ায়। রাজনীতিকে আমরা রাজরাজড়াদের নীতিতেই পরিণত করেছি, নামে যেমন কাজেও তেমনি। ব্রাহ্মণরাই এ নিয়ে মাথা ঘামাবে; শূদ্ররা তাদের নিজেদের স্বাভাবিক কাজে। অর্থাৎ উৎপাদনশীল শ্রমে ব্যস্ত থাকে। বিধান এমনই। যার যেটা সাজে। এবং এমনও প্রচার করা হয়েছে, হচ্ছে প্রকাশ্যে কখনও, অপ্রত্যক্ষরূপে অধিকাংশ সময়ে– প্রজা যেমন রাজাও তেমনি। হতে বাধ্য। নাগরিকরা তেমন সরকারই পেয়ে থাকে যেমনটা নাকি তাদের প্রাপ্য– বক্তব্য দাঁড়ায় এ রকমেরই। অর্থাৎ দোষ শাসক শ্রেণির নয়, দোষ হচ্ছে প্রজাদের। তারা পাপ করেছে, এখন ফল ভোগ না করে উপায় কী? এ জন্মে না করলেও পাপ পূর্বজন্মে করে থাকবে। ঝরনার পানি তুমি না ঘোলা করে থাকলে তোমার বাপ ঘোলা করেছে।
অথচ একেবারে স্পষ্ট সত্য তো এটাই, বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা জনগণ তৈরি করেনি; ষড়যন্ত্র করে এটা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এটি কাঁধের ওপর চেপে বসে রয়েছে। ফেলে দেওয়া দরকার ছিল; কিন্তু ফেলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ হচ্ছে ওই মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা সমালোচনা করে ঠিকই কিন্তু বৈপ্লবিক পরিবর্তন চায় না। চায় না এই ভয়ে যে, তাতে তাদের সুযোগ-সুবিধা ভেস্তে যাবে। তারা নিজেরা মিশে যাবে হতশ্রী গরিব মানুষের দলে।
বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। হবার কথা ছিল, হয়নি। এই রাষ্ট্র একটি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, যার প্রবণতা ফ্যাসিবাদ অভিমুখী। ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদেরই একটি অসহিষ্ণু ও উগ্র রূপ। পুঁজিবাদের পবিত্রটাই হচ্ছে অসামাজিক; সে সমাজকে নিয়ে ভাবে না, ব্যক্তিকে উৎসাহিত করে যেমন করে পারো ধনী হতে। মানুষ যদি রাজনীতিবিমুখ হয় তাহলে পুঁজিবাদের ভারি সুবিধা। তার শোষণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে তখন কোনো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে উঠবে না, এমনকি দরকষাকষিও রইবে না। পুঁজিবাদ তার অসামাজিক তৎপরতা নির্বিরোধে চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে।
বিশ্বজুড়ে এখন চলছে অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগ। আমরাও উত্তেজিত হচ্ছি। গ্রামে ফোন চলে গেছে, ঘরে ঘরে ইন্টারনেট ব্যস্ত রয়েছে; উপগ্রহের মধ্য দিয়ে টেলিভিশনের বহুবিধ ছবি দেখছি। যেন বিপ্লবই ঘটে গেছে। আসলে বিপ্লব-টিপ্লব নয়। যা ঘটেছে তা নতুন শুধু রূপেই, মর্মবস্তুতে সেই পুরাতন বস্তু। এ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, তথ্যের সাম্রাজ্যবাদ। পুঁজিবাদী বিশ্ব যা সরবরাহ করছে। তথ্য তাদের, ব্যাখ্যাও তাদেরই। সঙ্গে থাকছে আদর্শ, যেটা খুবই জরুরি। তথ্যের ওই তথাকথিত অবাধ প্রবাহ আমাদেরকে আদর্শগতভাবে সাম্রাজ্যবাদের অনুরাগী ও অধীনস্থ করে তুলছে। মস্তিষ্ক ভরে যাচ্ছে আদর্শিক আবর্জনায়। বিকৃত হচ্ছে বোধশক্তি।
আমরা সারাবিশ্বের খবর শুনছি, দেখছি, পড়ছি। যেন রূপকথার কাহিনি। এসব গালগল্প ওইসব রূপকথার রাজা-রানী, নায়ক-নায়িকাদের হাঁচি-কাশি নর্তন-কুর্দন সবকিছু সম্পর্কে জানাচ্ছে, কিন্তু পৃথিবীটাকে বুঝতে এতটুকু সাহায্য করছে না। পৃথিবীটাকে বদলাবার যে স্বপ্ন, হাসতে হাসতে তাকে কেড়ে নিচ্ছে। তথাকথিত অনুন্নত বিশ্বের মানুষ আমরা পরিণত হচ্ছি তথাকথিত উন্নত বিশ্বের হাতের পুতুলে। বাড়ছে না দর্শনের চর্চা। যন্ত্রপাতি আসছে কিছু কিছু, কিন্তু বিজ্ঞান আসছে না। পুঁজিবাদ মানুষকে দার্শনিক হতে উৎসাহিত করে না, প্রলুব্ধ করে ভোগবাদী হতে। তার যত প্রচার, যত বিজ্ঞাপন সবই ভোগবাদিতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে। সে পণ্যের ক্রেতা চায়, ভাবুক মানুষ চায় না। যন্ত্রপাতি বিক্রি করে। রাষ্ট্রকে উদ্বুদ্ধ করে সমরাস্ত্র ক্রয়ে; ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করে ব্যবহারিক সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে ঘরবাড়ি ঠেসে ভরে ফেলতে। পুঁজিওয়ালাদের তাতে মুনাফা বাড়ে। এসবের মধ্য দিয়ে যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা হলো, দেশের ভেতরে মানুষের জন্য সবচেয়ে কঠিন যে অভিশাপ সেই বৈষম্য। অন্যদিকে দুর্বল রাষ্ট্রগুলো চলে যাচ্ছে বিশ্ব পুঁজিবাদের একেবারে হাতের মুঠোয়। তাদের স্বাধীনতা নামেই শুধু; তারা পরিণত হচ্ছে ক্রীড়নকে।
সাম্রাজ্যবাদ এখন নাম নিয়েছে বিশ্বায়নের। বিশ্বকে সে একটি গ্রামে পরিণত করবে এবং সেটাই করছে বটে। ধনী দেশ থেকে রপ্তানি পণ্যের চলাফেরা বাধা মানবে না; কিন্তু গরিব দেশের পণ্য বাধাগ্রস্ত হবে শুল্ক দ্বারা। কখনও কখনও সেই পণ্যে দুর্গন্ধ পাওয়া যাবে শিশুশ্রমের, কখনও মানবাধিকার-বঞ্চনার। ছাঁটাই হবে শ্রমিক। বাড়বে বেকারত্ব। ছড়িয়ে পড়বে হতাশা। দেখা দেবে মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস ও মৌলবাদ। যার লক্ষণ এখন উৎকটভাবেই দৃশ্যমান। ওদিকে শ্রমের অবাধ চলাফেরা থাকবে না। তাকে রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করে ধনী বিশ্বে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। হবে না। বলা হবে, কাজটা অবৈধ। অনুপ্রবেশকারী তৎপরতা।
বিশ্বায়নকে বলা হচ্ছে আধুনিক; কিন্তু আধুনিকতার উপাদান যে দুটি, তার কোনোটিই এতে উপস্থিত নেই। চিরকালই আধুনিকতার একটি উপাদান হচ্ছে দার্শনিক জিজ্ঞাসা, অপরটি আন্তর্জাতিকতা। বিশ্বায়ন এই দুইয়ের কোনটিকেই উৎসাহিত করে না। মানুষ যতই উদাসীন থাকে, যতই অজ্ঞ থাকে বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে, তাকে শোষণ করার ব্যাপারে ততই সুবিধা। বিশ্বায়ন তার নিজের জন্য ওই সুবিধা তৈরি করতে ব্যস্ত। মানুষের ভোগলিপ্সাকে উস্কে দিয়ে তার মস্তিষ্ককে নিষ্ক্রিয় ও আবর্জনায় ভরপুর করে রাখতে সে সর্বদাই সচেষ্ট।
বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিকতা মোটেই এক বস্তু নয়, বরং পরস্পরবিরোধী। বিশ্বায়ন হচ্ছে পুঁজি ও পণ্যের আন্তর্জাতিকতা; তার মধ্যে বিশ্বজনীনতার নাম-নিশানা নেই, সর্বজনীনতার তো নয়ই। কেননা, সে হচ্ছে মুনাফানির্ভর। তার লক্ষ্য বাণিজ্য। অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতা হচ্ছে বিশ্বের দেশে দেশে মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। যার ভিত্তি সহমর্মিতা ও মর্যাদাবোধ। আন্তর্জাতিকতা বিশ্বকে ছোট করতে চায় না। বিশ্বের বৈচিত্র্য রক্ষা করাই তার ইচ্ছা। সে চায় মানবিক সহযোগিতা, চায় পারস্পরিক সম্মানভিত্তিক ঐক্য। আন্তর্জাতিকতা আসলে বিশ্বায়নের প্রতিপক্ষ। এ যত এগোবে ও তত পেছাবে। ঘটছেও তাই। শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক আন্দোলন এখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে ঠিকই; কিন্তু তা দানা বেঁধেও উঠছে বৈকি। উঠতে বাধ্য। বিশ্বায়নই বাধ্য করবে মানুষকে বিক্ষুব্ধ হতে এবং বিক্ষুব্ধ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে। তবে তার চেষ্টা হবে মানুষকে চিত্তবিমুখ ও দেহসর্বস্ব করে রাখা।
লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়